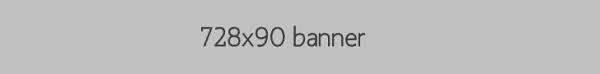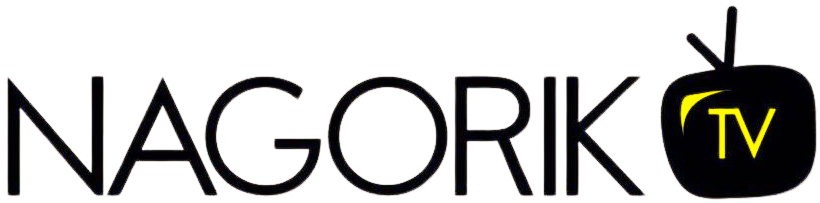মিয়ানমার সংকট, আরাকান ফ্যাক্টর ও ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের ভূমিকাপত্র
এই বাস্তবতায় ভারত স্বভাবতই শঙ্কিত। কারণ ইউনুসের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের অভ্যন্তরেও ‘সফট পাওয়ার’ হিসেবে কাজ করতে পারে!

প্রকাশিত : ২৪ এপ্রিল ২০২৫, ১০:৫৬:৪২
মিয়ানমারের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামরিক সংকট, বিশেষ করে আরাকান আর্মির তৎপরতা এবং জান্তা সরকারের বিপর্যস্ত অবস্থান, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতিকে নতুন এক মোড়ে নিয়ে গেছে। এই সংকটের কেন্দ্রে এখন যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র—এই চারটি রাষ্ট্রের সমীকরণ বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।
ভারত ও উত্তর-পূর্ব নিরাপত্তা বাস্তবতা:
ভারতের জন্য মিয়ানমার কেবলমাত্র একটি প্রতিবেশী নয়; বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের অস্তিত্বের সাথে জড়িত একটি কৌশলগত গেটওয়ে। এই এলাকাগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিগত সংঘাত এবং চীনা প্রভাবের আশঙ্কায় বহুদিন ধরেই অস্থির। মিয়ানমারের ভূভাগে আরাকান আর্মির আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে যেহেতু আরাকান আর্মির কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে চীনের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
অন্যদিকে, ভারত মিয়ানমার জান্তা সরকারকে সমর্থন করেও এখন অনেকটা বিব্রত। তাদের একদিকে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোয় শান্তি দরকার, আবার অন্যদিকে আরাকান ও চট্টগ্রাম উপকূলবর্তী বাণিজ্যিক করিডোরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বৈত চাপে ভারত এখনো তার অবস্থান খোলাখুলি প্রকাশ করছে না, তবে গোয়েন্দা ও সেনা পর্যায়ে একাধিক প্রস্তুতি চলছে বলেই অনুমান।
যুক্তরাষ্ট্র ও “ডিপ সাউথ স্ট্র্যাটেজি”:
যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এখন আর তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই। মিয়ানমারে আরাকান অঞ্চল ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র একটি বিকল্প ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে, যা তাদের জন্য একাধারে চীন সীমান্তের নজরদারি, বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক প্রভাব এবং রোহিঙ্গা ইস্যুর মানবিক চাপ ব্যবস্থাপনার সুযোগ এনে দিতে পারে।
বাংলাদেশ, যেহেতু আরাকান সীমান্তে সরাসরি অবস্থান করছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে—চাইলেও না চাইলেও। বিশেষ করে যদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ও “মানবিক করিডোর” তৈরির মতো উদ্যোগ নেয়, তাহলে তা চীনের দৃষ্টিতে একটি সুস্পষ্ট “লক্ষ্যভেদ” হয়ে উঠতে পারে।
চীন ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ:
সাম্প্রতিক সময়ে চীন বাংলাদেশকে যে ধরনের প্রযুক্তিসম্পন্ন যুদ্ধবিমান, নজরদারি ড্রোন, এবং সাইবার সুরক্ষা সরঞ্জাম দিচ্ছে, তা শুধু প্রতিরক্ষা নয় বরং ‘স্ট্র্যাটেজিক এলায়েন্স’-এর প্রতীক। চীনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট: বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় বেষ্টিত অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখা।
চীন জানে, ভারতের মতো বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যেও একটি সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ভূমিকা রয়েছে। এই ‘মিলিটারি-সেন্ট্রিক স্টেট মেকানিজম’ চীনের কাছে অধিক বিশ্বাসযোগ্য, কারণ রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তন হলেও সামরিক কৌশল একরকম ধারাবাহিক থাকে। তাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলা চীনের কৌশলের অন্যতম স্তম্ভ।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কি নতুন মিশনে ইনগেজড?
সম্প্রতি বিভিন্ন উৎস থেকে মিলেছে যে, সেনাবাহিনী শুধুমাত্র সীমান্ত রক্ষার জন্য নয়, বরং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য একটি 'স্ট্যাবিলাইজেশন অপারেশন'-এর ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছে। যদি সত্যি আরাকান আর্মির সঙ্গে অঘোষিত সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো 'সেফ জোন' তৈরি হয়, তবে সেটি জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতে পারে।
একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে—বাংলাদেশ তার ভূকৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক 'স্মার্ট ব্যালেন্সিং'-এর পথে হাঁটছে, যেখানে মানবিকতা, নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক ন্যায়বিচারের ফ্রেমওয়ার্কে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হবে।
ডঃ ইউনুস ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ম্যাট্রিক্সে ভারসাম্য:
ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস কেবলমাত্র অর্থনীতিবিদ বা শান্তির দূত নন; বরং তিনি একটি আদর্শের প্রতীক। আন্তর্জাতিক ফোরামে তার গ্রহণযোগ্যতা পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর একটি বিকল্প ভরসার জায়গা তৈরি করে। দক্ষিণ এশিয়ায় যেখানে গণতন্ত্র ক্রমশ হিন্দুত্ববাদী ও কর্তৃত্ববাদী ধারায় এগোচ্ছে, সেখানে ইউনুসের মতো ক্যারিশমেটিক ব্যক্তিত্ব একটি “অসাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ” হিসেবে মূল্যায়িত হচ্ছেন।
এই বাস্তবতায় ভারত স্বভাবতই শঙ্কিত। কারণ ইউনুসের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের অভ্যন্তরেও ‘সফট পাওয়ার’ হিসেবে কাজ করতে পারে। ভারত চাইবে না, কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 'অল্টারনেটিভ প্রজেকশন' তৈরি করুক।